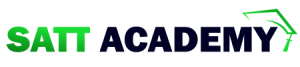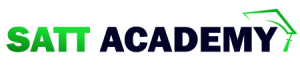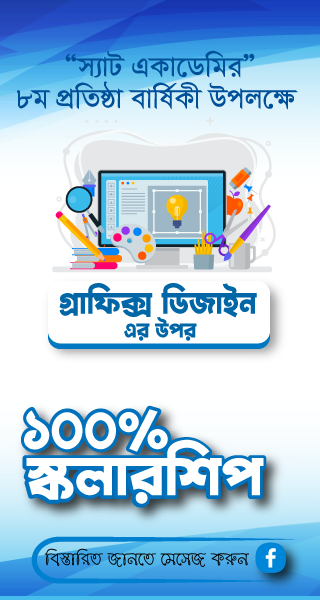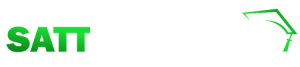১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। নয় মাস পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে ১৬ ডিসেম্বর আমাদের দেশ শত্রুমুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্বের, গৌরবের কাহিনি। বাঙালি জাতির এমন অনেক গৌরবের কাহিনি আছে। সেসব জানতে হলে ইতিহাস পড়তে হবে, চর্চা করতে হবে। ইতিহাস সত্য ঘটনা উপস্থাপন করে। ইতিহাস সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান করতে হলে ইতিহাসের উপাদান, প্রকারভেদ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।
এজন্য আগে আমাদের নামতে হবে ইতিহাস কী? জানতে হবে কত ধরনের ইতিহাস লেখা যার যা ইতিহাস কত ধরনের হয়। ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তাই বা কী? এই অধ্যায়ে এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং
এই অধ্যায় শেষে আমরা -
• ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারণা, স্বরূপ ও পরিসর ব্যাখ্যা করতে পারব;
• ইতিহাসের উপাদান ও প্রকার বর্ণনা করতে পারব;
• ইতিহাস পাঠের প্রজোজনীয়তা আলোচনা করতে পারব;
• ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহী হব ।
হেরোডোটাস
লিওপোল্ড ফন র্যাংক
টয়েনবি
ই. এইচ. কার
‘ইতিহাস' শব্দটির উৎপত্তি ‘ইতিহ' শব্দ থেকে; যার অর্থ 'ঐতিহ্য'। ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে । এই ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় ইতিহাস। ই. এইচ. কার-এর ভাষায় বলা যায়, ইতিহাস হলো বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ ।
বর্তমানের সকল বিষয়ই অতীতের ক্রমবিবর্তন ও অতীত ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আর অতীতের ক্রমবিবর্তন ও ঐতিহ্যের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণই হলো ইতিহাস । তবে এখন বর্তমান সময়েরও ইতিহাস লেখা হয়, যাকে বলে সাম্প্রতিক ইতিহাস । সুতরাং ইতিহাসের পরিসর সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত ।
ইতিহাস শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে এরূপ দাঁড়ায়, ইতিহ + আস । যার অর্থ এমনই ছিল বা এরূপ ঘটেছিল । ঐতিহাসিক ড. জনসনও ঘটে যাওয়া ঘটনাকেই ইতিহাস বলেছেন । তাঁর মতে, যা কিছু ঘটে তাই ইতিহাস। যা ঘটে না তা ইতিহাস নয় ।
গ্রিক শব্দ ‘হিস্টরিয়া (Historia) থেকে ইংরেজি হিস্টরি (History) শব্দটির উৎপত্তি, যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ইতিহাস। 'হিস্টরিয়া' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক)। তিনি ‘ইতিহাসের জনক' হিসেবে খ্যাত। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর গবেষণাকর্মের নামকরণে এ শব্দটি ব্যবহার করেন, যার আভিধানিক অর্থ হলো সত্যানুসন্ধান বা গবেষণা। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইতিহাস হলো- যা সত্যিকার অর্থে ছিল বা সংঘটিত হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা ও লেখা। তিনি তাঁর গবেষণায় গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করেছেন । এতে তিনি প্রাপ্ত তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং গ্রিসের বিজয়গাথা লিপিবদ্ধ করেছেন । যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এ ঘটনা ভুলে না যায়, এ বিবরণ যেন তাদের উৎসাহিত করে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে । হেরোডোটাসই প্রথম ইতিহাস এবং অনুসন্ধান— এ দুটি ধারণাকে সংযুক্ত করেন । ফলে ইতিহাস পরিণত হয় বিজ্ঞানে, পরিপূর্ণভাবে হয়ে ওঠে তথ্যনির্ভর এবং গবেষণার বিষয়ে । প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের অনন্ত ঘটনাপ্রবাহই হলো ইতিহাস। ইতিহাসবিদ র্যাপসন বলেছেন, ইতিহাস হলো ঘটনার বৈজ্ঞানিক এবং ধারাবাহিক বর্ণনা ।
আধুনিক ইতিহাসের জনক জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ফন্ র্যাংকে মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তার অনুসন্ধান ও তার সত্য বিবরণই ইতিহাস । সুতরাং ইতিহাস হচ্ছে মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণ । সঠিক ইতিহাস সবসময় সত্যকে নির্ভর করে রচিত ।
যেসব তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তাকেই ইতিহাসের উপাদান বলা হয় । ইতিহাসের উপাদানকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা : লিখিত উপাদান ও অলিখিত উপাদান ।
১. লিখিত উপাদান: ইতিহাস রচনার লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ইত্যাদি । বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সাহিত্যকর্মেও তৎকালীন সময়ের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যেমন : বেদ, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী, মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তবকাত-ই-নাসিরী', আবুল ফাল-এর 'আইন-ই-আকবরী' ইত্যাদি। বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ সব সময়ই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন- পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে বাংলায় আগত চৈনিক পরিব্রাজক যথাক্রমে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইংসিং-এর বর্ণনা। পরবর্তী সময়ে আফ্রিকান পরিব্রাজক ইবনে বক্তৃতাসহ অন্যদের লেখাতেও এ অঞ্চল সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। এসব বর্ণনা থেকে তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যान । সাহিত্য উপাদানের মধ্যে আরও রয়েছে রূপকথা, কিংবদন্তি, গল্পকাহিনি। তিব্বতীয় লেখক লামা তারনাথের বর্ণনায় পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের সিংহাসন আরোহণ সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে, সেটি একধরনের কল্পকাহিনি। তবে অনেক কাহিনির আড়ালে অনেক সত্য ঘটনা থেকে যায় যা ঐতিহাসিকরা বিচার- বিশ্লেষণ-অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করেন। তাছাড়া সরকারি নথি, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকেও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব। ইতিহাসের উপাদান
২. অলিখিত বা প্রত্নতত্ত্ব উপাদান : যেসব বস্তু বা উপাদান থেকে আমরা বিশেষ সময়, স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাই, সেই বস্তু বা উপাদানই প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন। প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনসমূহ মূলত অলিখিত উপাদান। যেমন : মুদ্রা, শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, তাম্রলিপি, ইমারস্ক ইত্যাদি। এ সমস্ত প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের ফলে সে সময়ের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ধারণা করা সম্ভব প্রাচীন অধিবাসীদের সভ্যতা, ধর্ম, জীবনযাত্রা, নগরায়ণ, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে । উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় সিন্ধু সভ্যতা, বাংলাদেশের মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি ইত্যাদি স্থানের প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনের কথা। নতুন নতুন প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার বদলে দিতে পারে একটি জাতির ইতিহাস। যেমন- সম্প্রতি নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কার। ঐ অঞ্চলের প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শনে প্রমাণ হয়েছে যে, বাংলাদেশে আড়াই হাজার বছর পূর্বেও নগর সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। এই আবিষ্কারের ফলে বাংলার প্রাচীন সভ্যতার নবদিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে বাংলার প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে অনেক ধারণা। অদূর ভবিষ্যতে নতুন ভাবে লিখতে হবে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ।
| একক কাজ : ইতিহাসের বিভিন্ন ধরনের উপাদানের একটি তালিকা কর । |
মানব সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বিষয়ের ইতিহাস লেখা হচ্ছে। ফলে সম্প্রসারিত হচ্ছে ইতিহাসের পরিসর । ইতিহাস বিরামহীনভাবে অতীতের ঘটনা বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় । সেক্ষেত্রে ইতিহাসকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা কঠিন । তাছাড়া ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে মানুষ, মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও জীবনধারা পরস্পর সম্পৃক্ত এবং পরিপূরক । তারপরও পঠন-পাঠন, আলোচনা ও গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে ইতিহাসকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় ৷ যথা— ভৌগোলিক অবস্থানগত ও বিষয়বস্তুগত ইতিহাস ।
১. ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক বা ভৌগোলিক অবস্থানগত ইতিহাস : যে বিষয়টি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তা কোন প্রেক্ষাপটে রচিত— স্থানীয়, জাতীয় না আন্তর্জাতিক? এভাবে ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে শুধু বোঝার সুবিধার্থে ইতিহাসকে আবারও তিন ভাগে ভাগ করা যায় যথা— স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস ।
২. বিষয়বস্তুগত ইতিহাস : কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যে ইতিহাস রচিত হয়, তাকে বিষয়বস্তুগত ইতিহাস বলা হয় । ইতিহাসের বিষয়বস্তুর পরিসর ব্যাপক । তবু সাধারণভাবে একে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা— রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ইতিহাস ।
মানবসমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তনের প্রমাণ ও লিখিত দলিল হলো ইতিহাস। ঐতিহাসিক ভিকো (Vico) মনে করেন, মানব সমাজ ও মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশই ইতিহাসের বিষয়বস্তু । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যা মানব সমাজ-সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে, তা সবই ইতিহাসভুক্ত বিষয় । যেমন- – শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, ধর্ম, আইন প্রভৃতি বিষয়, সামগ্রিকভাবে যা কিছু সমাজ-সভ্যতা বিকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে, তা-ই ইতিহাসের বিষয়বস্তু ।
ইতিহাস জ্ঞান অর্জনের অন্যান্য শাখা থেকে আলাদা। এর রচনা ও উপস্থাপনার পদ্ধতিও ভিন্ন। ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করলে এ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।
- প্রথমত, সত্যনিষ্ঠ তথ্যের সাহায্যে অতীতের পুনর্গঠন করাই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য।
- দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের আলোচনার বিষয় হচ্ছে মানবসমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক তথ্যনির্ভর বিবরণ।
- তৃতীয়ত, ইতিহাস থেমে থাকে না, এটি গতিশীল এবং বহমান। যে কারণে প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ, আধুনিকযুগ সন তারিখ ব্যবহার করে ভাগ করা কঠিন। আবার পরিবর্তনের ধারাও সব দেশে একসঙ্গে ঘটেনি।
- চতুর্থত, ঘটে যাওয়া ঘটনার সঠিক বিবরণ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাও ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। তবে ঘটনার নিরপেক্ষ বর্ণনা না হলে সেটা সঠিক ইতিহাস হবে না ।
| একক কাজ : সত্যনিষ্ঠ তথ্যের সাহায্যে অতীতকে পুনর্গঠন করাই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য— ব্যাখ্যা কর । |
মানুষ কর্তৃক সম্পাদিত সকল বিষয় ইতিহাসের আওতাভুক্ত। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, কার্যক্রম- যত শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত, ইতিহাসের সীমাও ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। যেমন- প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বের মানুষের কর্মকাণ্ড খাদ্য সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে সে সময় ইতিহাসের পরিসরও খাদ্য সংগ্রহমূলক কর্মকাণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস চর্চা ও গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। ফলে ইতিহাসের শাখা- প্রশাখার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, বিস্তৃত হচ্ছে ইতিহাসের সীমানাও। উনিশ শতকে শুধু রাজনীতি ইতিহাসের বিষয় হলেও মার্কসবাদ প্রচারের পর অর্থনীতি, সমাজ, শিল্পকলার ইতিহাসও রচিত হতে থাকে। এভাবে একের পর এক বিষয় ইতিহাসভুক্ত হচ্ছে আর সম্প্রসারিত হচ্ছে ইতিহাসের পরিধি ও পরিসর।
মানবসমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের সত্য-নির্ভর বিবরণ হচ্ছে ইতিহাস । এ কারণে জ্ঞানচর্চার শাখা হিসেবে ইতিহাসের গুরুত্ব অসীম । ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে, ভবিষ্যৎ অনুমান করতে সাহায্য করে । ইতিহাস পাঠের ফলে মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজদেশ সম্পর্কে মঙ্গল-অমঙ্গলের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব । সুতরাং দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং ব্যক্তি প্রয়োজনে ইতিহাস পাঠ অত্যন্ত জরুরি ।
- জ্ঞান ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে : অতীতের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে । আর এ বিবরণ যদি হয় নিজ দেশ-জাতির সফল সংগ্রাম ও গৌরবময় ঐতিহ্যের, তাহলে তা মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে । একই সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে । সে ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ, জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণে ইতিহাস পাঠের বিকল্প নেই ।
- সচেতনতা বৃদ্ধি করে : ইতিহাস - জ্ঞান মানুষকে সচেতন করে তোলে । উত্থান-পতন এবং সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানতে পারলে মানুষ ভালো-মন্দের পার্থক্যটা সহজেই বুঝতে পারে । ফলে সে তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে ।
- দৃষ্টান্তের সাহায্যে শিক্ষা দেয় : ইতিহাসের ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম । মানুষ ইতিহাস পাঠ করে অতীত ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে পারে । ইতিহাসের শিক্ষা বর্তমানের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে । ইতিহাস দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেয় বলে ইতিহাসকে বলা হয় শিক্ষণীয় দৰ্পন ।
ইতিহাস পাঠ করলে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, যা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সাহায্য করে । ফলে জ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ জন্মে ।
| দলীয় কাজ : তোমার এলাকার অথবা কাছাকাছি কোনো ঐতিহাসিক স্থান/নিদর্শন পরিদর্শন করে তার ঐতিহাসিক উপাদানগুলো চিহ্নিত কর । |